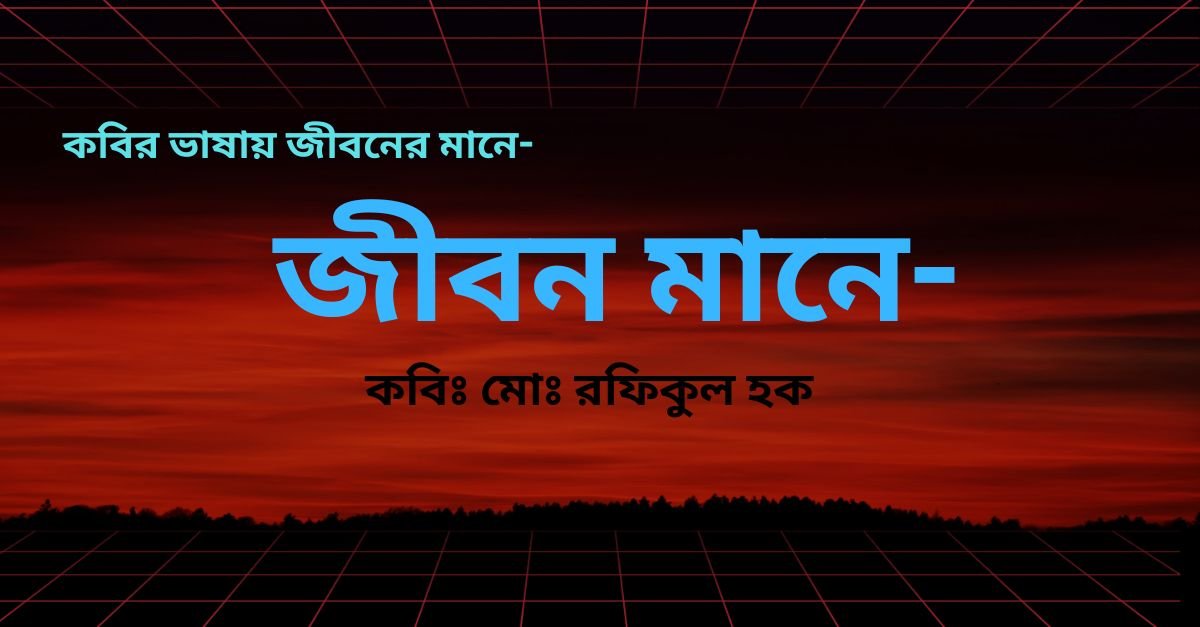চর্যাপদ
চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রাচিন যুুুগের একমাত্র নিদর্শন যা মূলত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাধন সঙ্গিত। চর্যাপদে সহজিয়া পণ্ডিতগণ নিজেদের সাধনার অংশ হিসেবে; বৌদ্ধধর্মের গূঢ় সাধনাপ্রণালী ও দর্শনতত্ত্ব নানা প্রকার রুপকের মাধ্যমে এখানে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যাক্ত করেছেন। চর্যাপদ কবিতা সংকলন হিসেবে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।
চর্যাপদের আবিস্কার
চর্যাপদের আবিস্কর্তা হলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি। তিনি ১৯০৭ সালে নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে পুঁথিটি আবিস্কার করেন। ১৯০৭ সালের আগে চর্যাপদ সম্পর্কে কোন তথ্যই জানা ছিল না। ১৮৮২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ‘Sanskrit Buddhist Literature in Nepal’ গ্রন্থে প্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা তুলে ধরেন। এই গ্রন্থের বিবরণী থেকে উদ্দীপ্ত হয়ে এবং তৎকালীন বৃটিশ সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্র্রি নেপালে তৃতীয় অনুসন্ধান সফর কালে নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব– এর পদগুলো আবিষ্কার করেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চারটি পুঁথি একত্রিত করে ’হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে একমাত্র ’চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ প্রাচীন বাংলায় লেখা অন্য তিনটি গ্রন্থ অপভ্রংশ ভাষায় রচিত।
চর্যাপদের রচনাকাল
চর্যাপদ পাল আমলের সৃষ্টিকর্ম। পণ্ডিতগণ সঙ্গত কারনেই, চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে মতৈকে পৌছাতে না পারলেও ধরে নেওয়া হয় সপ্তম শতাব্দী হতে দশম/দ্বাদশ শতাব্দির মধ্যবর্তী সময়ে চর্যার পদগুলো রচিত হয়। চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে বিভিন্ন মণিষিদের মতবাদ নিম্নরুপ:
১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের রচনাকাল: ৬৫০ – ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ।
২. ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের রচনাকাল: ৯০০ – ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ।
৩. ড. সুতিতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, চর্যাপদের রচনাকাল: ৯৫০ – ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ
চর্যাপদের ভাষা
চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষা তাতে কোন সন্দেহ নেই। চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এবং এর ভাষা দুর্বোদ্ধ। চর্যাপদ যখন রচিত হয় তখনও বাংলা আজকের মতো স্বতন্ত্র কোন ভাষায় পূর্ণতা পায় নি এবং এবং এতে গৌড় অপ্রভংশের প্রভাব রয়েছে। তাই কেউ কেউ একে অপ্রভংশ, প্রাচীন হিন্দি, মৈথিলি, উড়িয়া বা আসামি বলে দাবি করেন।
সন্ধ্যাভাষা:
কারো কারো মতে চর্যাপদের ভাষা ’সন্ধ্যাভাষা’। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-এর মতে, ‘চর্যাপদের আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।”
চর্যাপদের কবি
চর্যাপদের কবির সংখ্যা ২৪ (মতান্তরে ২৩) জন। গানের মাঝে বা শেষে তাঁরা ভণিতা দিয়েছেন। তাদের নামের শেষে গৌরবসূচক ‘পা’ যোগ করা হয়েছে। এঁরা হলেন: লুই পা, কুক্কুরী পা, বিরুপ পা, গুণ্ডরী পা, চাটিল্ল, ভুসুক পা, কাহ্ণ পা, কম্বলাম্বর পা, ডোম্বী পা, শান্তি পা, মহীত্তা পা, বীণা পা, সরহ পা, তন্ত্রী পা, শবর পা, আর্যদেব, ঢেণ্ঢন পা, দারিক পা, ভাদে পা, তারক পা, কঙ্কণ পা, জঅনন্দী পা, ধর্ম পা, লাড়িডোম্বি পা।
এসব নামের কতগুলো ছদ্মনাম এবং তন্ত্রী পা ও লাড়ীডোম্বী পা- এর কোন পদ পাওয়া যায় নি। চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহ্ণ পা- তিনি ১৩টি পদ রচনা করেন। অনেকের মতে প্রথম/ আদি কবি লুই পা।
লুই পা
চর্যাপদের প্রথম কবিতা লুইপার লেখা। লুই পা চর্যাপদের ১নং ও ২৯ নং পদ রচনা করেছেন। অনেকে মনে করেন, লুই পা চর্যাকারদের মধ্যে প্রবিণতম এবং আদি চর্যাকার। সেজন্য লুইপাকে বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বলা হয়। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর তাঁকে প্রথম কবি বলে স্বীকার করেন না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে লুই পার জীবনকাল ৭৩০-৮১০ সাল।
লুইপা রচিত চর্যাপদের প্রথম কবিতা-
কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুখ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।
সঅল সহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই।।
এরি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপথ ভিতি লেহু রে পাস।।
ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিত্তি বইঠা।।
আধুনিক অর্থ: শ্রেষ্ঠ তরু এই শরীর এবং তার পাঁচটি ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করে। চিত্তকে দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও সমস্ত সমাধি কেন করা হয়। সুখে দুখে সে নিশ্তিত মারা যায়। ছলবন্ধ কপট ইন্দ্রিয়ের আশা ত্যাগ কর। শূণ্যতা পক্ষে ভিড়ে পার্শ্বে নাও। লুই বলেন, আমি ধমন চমন দুই পিঁড়িতে বসে ধ্যানে দেখেছি।
কুক্কুরী পা
কুক্কুরী পা চর্যাপদের ২, ১৮ ও ২০ নং পদ রচনা করেন। তাঁর ৪৮ নং পদটি পাওয়া যায় নি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, কুক্কুরী পা বাংলাদেশের লোক এবং অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন। তিনি ইন্দ্রভুতির অন্যতম গুরু। কুক্কুরী পা কপিলাবস্তুতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে মহিলা কবি মনে করা হয়।
২নং পদের প্রথম দুটি চরণ হলো:
দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ।।
আধুনিক বাংলা:
কচ্ছপ দুয়ে পাত্রে ধরা না যায়। গাছের তেতুল সবই কুমিরে খায়।।
গুঢ়ার্থ: অপরিশুদ্ধ চিত্তে পরমাত্মাকে ধারণ করা যায় না। দেহের ইন্দ্রিয়াদি সবকিছু বিনাশ করে দেয়।
বিরুপ পা
বিরুপ পা চর্যাপদের ৩নং পদটি রচনা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, বিরুপ পা ছিলেন জলান্ধরী পার শিষ্য এবং তাঁর জন্ম দেবপালের রাজ্য ত্রিপুরায়। বিরুপ পা অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন। এবং তাঁর জীবনকালের শেষ সীমা ৮৩০ সাল। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, বিরুপ পা ভিক্ষুরুপে সোমপুর বিহারে বাস করতেন।
গুণ্ডরী পা
গুণ্ডরী পা চর্যাপদের ৪নং পদটি রচনা করেন। তিনি দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তাঁর জীবনকালের নিম্নসীমা ৮৪০ সাল এবং জন্মস্থান ডীশুনগর। গুণ্ডরীপা তাঁর বৃত্তি বাচক নাম তিনি বর্ণে ছিলেন কর্মকার ও সিদ্ধা।
চাটিল পা
চাটিল পা চর্যাপদের ৫নং পদটি রচনা করেন এবং দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কবিতায় সাঁকো এবং নদীমাতৃক অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। চাটিল পা ৮৫০ সালের দিকে বর্তমান ছিলেন।
ভুসুক পা
ভুসুক পা মোট আটটি পদ রচনা করেন এবং চর্যার সংখ্যাধিক্যের বিচারে তাঁর অবস্থান দ্বিতীয়। তিনি চর্যাপদের ৬, ২১, ২৩ (অর্ধেক প্রাপ্ত),২৭, ৩০, ৪১, ৪৩,৪৯নং পদ রচনা করেন। নানা কিংবদন্তি বিচারে ভুসুকু পা নামটি ছদ্মনাম মনে করা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম শান্তিদেব। তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজা কল্যাণবর্মার পুত্র ছিলেন এবং শেষ জীবনে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নালন্দায় অবস্থান করেন। তাঁর জীবনকালের শেষ সীমা ৮০০ শতাব্দি।
ভুসুকু পা রচিত চর্যার নমুনা:
কাহৈরি ঘিনি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেটিল ডাক পড়অ চৌদীস।।
আপণা মাংসে হরীণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু আহেরী।।
আধুনিক বাংলা অর্থ: কাকে নিয়ে কাকে ছেড়ে কেমন করে আছি। চাড়পাশে হাঁক পড়ে। আপন মাংসের জন্যই হরিণ শত্রু। এক মুহূর্তের জন্যও শিকারি ভুসুকু ছাড়ে না।
কাহ্ণ পা
কাহ্ন পা মোট ১৩টি পদ রচনা করেন। চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে তিনি সর্বাধিক পদ রচনা করেছেন। বিভিন্ন পদে কাহ্ন কহ্নি, কাহ্নিলা, কাহ্নিল্য, কাহ্নূ, কাহ্নু প্রভৃতি ভণিতা লক্ষকরা যায়। তাঁর জন্ম উড়িষ্যায় এবং তাঁর জীবনের শেষ সীমা ৮৪০ সাল। কাহ্ন পা সোমপুর বিহারে বাস করতেন।
কাহ্ন পা রচিত চর্যার নমুনা:
এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িউ।
কাহ্ণ বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা।।
আধুনিক বাংলা অর্থ:
এবংকার দৃঢ় বন্ধন ভেঙ্গে এবং বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে আসবমত্ত কানু বিলাস করে। সে শান্ত হয়ে সহজ নলিনীবনে প্রবেশ করে।
ডোম্বি পা
ডোম্বি পা চর্যাপদের ১৪নং পদটি রচনা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, তিনি ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বিরুপ পা। ডোম্বি পার দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন এবং তাঁর জীবনকাল ৭৯০-৮৯০ পর্যন্ত। তিনি বর্ণে ক্ষত্রিয় ছিলেন।
মহীধর পা
মহীধর পা কাহ্নপার শিষ্য। তিনি চর্যাপদের ১৬নং পদটি রচনা করেন। তিনি মগধ অঞ্চলে বাস করতেন এবং তাঁর জীবৎকালের নিম্নসীমা ৮৭৫ সাল। মহীধর পা মগধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বর্ণে শূদ্র। তাঁর পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি।
বীণা পা
বীণা পা চর্যাপদের ১৬নং পদটি রচনা করেন। তিনি গৌড় অঞ্চলে জন্মকগ্রহণ করেন এবং তাঁর গুরুর নাম ছিল বুদ্ধ পা। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁর চর্যার ভাষা বাংলা।
সরহ পা
সরহ পা চর্যাপদের ২২,৩২,৩৮ ও ৩৯নং পদ রচনা করেছেন। সরহপার জন্মস্থান রাজ্ঞীদেশ বা উত্তরবঙ্গ-কামরূপ। কামরূপের রাজা রত্নপাল ছিলেন তাঁর শিষ্য।তিনি দশম-একাদশ শতকের কবি। তাঁর চর্যার ভাষা বঙ্গ-কামরূপী। সরহপা বর্ণে ব্রাহ্মণ ছিলেন।
তন্ত্রী পা
তন্ত্রী পা চর্যাপদের ২৫নং পদটি রচনা করেন কিন্তু তাঁর পদটি খুজে পাওয়া যায় নি।
শবর পা
শবর পা চর্যাপদের ২৮ ও ৫০নং পদ দুটি রচনা করেন। শবর পা ছিলেন বাঙালি এবং তিনি ছিলেন ব্যাধ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, তিনি চর্যার আদি পদকর্ত এবং লুইপার গুরু এবং নাগার্জুনের শিষ্য। তাঁর জীবনকাল ৬৮০-৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ।
আর্যদেব পা
আর্যদেব পা চর্যাপদের ৩১নং পদটি রচনা করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আজদেব। তারানাথের মতে, তিনি ছিলেন মেবারের রাজা এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য। তাঁর পদের ভাষা উড়িয়া।
ঢেণ্ঢণ পা
ঢেণ্ঢণ পা চর্যাপদের ৩৩নং পদটি রচনা করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ঢেণঢস। তাঁর জন্মস্থান অবন্তিনগর-উজ্জয়িনি, তিনি ছিলেন বর্ণে তাতী েএবং সিদ্ধা। তিনি দেবপাল-বিগ্রহপালের সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁর জীবনকালের উর্ধ্বসীমা ৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ।
ঢেণ্ঢণপা রচিত চর্যার নমুনা:
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।
আধুনিক বাংলা অর্থ: টিলার উপরে আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশি নেই। হাঁড়িত ভাত নেই, তবুও প্রতিদিন অতিথি আসে।
দারিক পা
দারিক পা চর্যাপদের ৩৪নং পদটি রচনা করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ইন্দ্রপাল। অনেকে মনে করেন, তিনি লুই পার শিষ্য। সে হিসেবে তাঁর সময়কাল অষ্টম শতকের শেষভাগ ও নবম শতকের প্রথমার্ধ। আবার অনেকে মনে করেন, উড়িষ্যার শালীপুত্রের রাজা ইন্দ্র পালই দাড়িক পা। তাঁর চর্যার ভাষা প্রাচীন বাংলা।
ভাদ্র পা
ভাদ্র পা বা ভাদে পা চর্যাপদের ৩৫নং পদটি রচনা করেন। তাঁর জন্মস্থান মহীভদ্র/ শ্রাবন্তী(রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে) এবং জীবনের নিন্মসীমা ৮৭৫ সাল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ভাদ্র পা কাহ্ন পার শিষ্য। তাঁর পদের ভাষা বাংলা।
তাড়ক পা
তারক পা চর্যাপদের ৩৭নং পদটি রচনা করেন। তাঁর সর্ম্পকে বিশেষ কিছু জানা যায় নি।
কঙ্কণ পা
কঙ্কণ পা চর্যাপদের ৪৪নং পদটি রচনা করেন। কেউ কেউ মনে করেন, তিনি কম্বলাম্বরের বংশধর ও দারিকের শিষ্য। প্রথম জীবনে তিনি বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন। তাঁর জীবনকাল নয় শতকের শেষভাগ। তাঁর রচিত পদটি বাংলা ও অপ্রভংশ মিশ্রিত।
জয়নন্দী পা
জয়নন্দী পা চর্যাপদের ৪৬নং পদটি রচনা করেন। তাঁর প্রকৃত নাম জয়ানন্দ। তিনি বাংলাদেশের এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন এবং বর্ণে ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর পদের ভাষা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রুপ।
ধর্ম পা
ধামপা বা ধর্মপা চর্যাপদের ৪৭নং পদটি রচনা করেন। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম এবং তিনি ছিলেন কাহ্ন পার শিষ্য। তাঁর জীবনকালের নিন্মসীমা ৮৭৫ সাল। তাঁর রচিত পদের ভাষা বাংলা।
লাড়ীডোম্বী পা
তাঁর কোন পদ পাওয়া যায় নি।