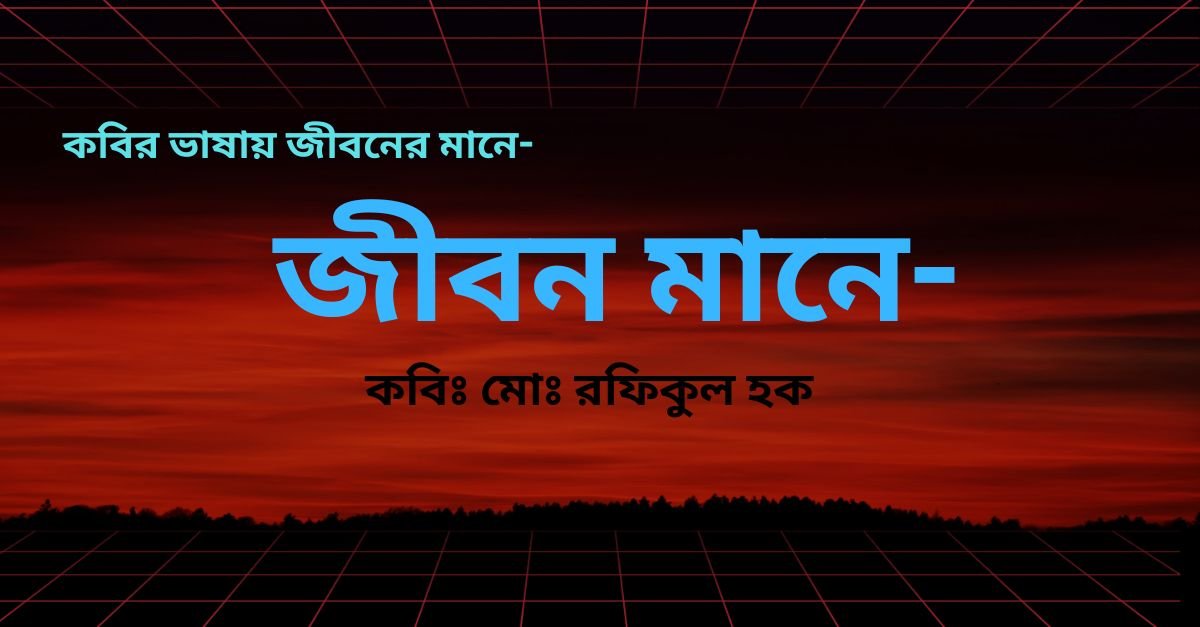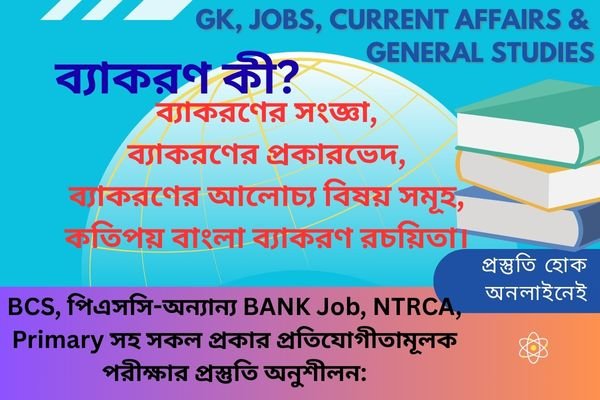সমাস:
সমাস শব্দের অর্থ সম্মিলন, সংক্ষেপণ বা বহুপদের একপদিকরণ। পরষ্পর অর্থ-সম্পর্কযুক্ত একাধিক শব্দের একত্রে মিলিত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করার প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।
যেমন: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন। দেশের সেবা = দেশসেবা। বিলাত হতে ফেরত = বিলাত-ফেরত ইত্যাদি।
সমাসের উদ্দেশ্য:
ভাষার সৈৗর্ন্দয ও সাবলীলতা বৃদ্ধি, নতুন শব্দ তৈরিকরণ ও বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস মূলত শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি।
সমস্ত পদ:
সমাসনিষ্পন্ন বা সমাসের প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ বা প্রাপ্ত নতুন শব্দটি-ই হলো সমস্ত পদ।
যেমন: সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা । এখানে, ’সাহিত্যসভা’ শব্দটি হলো সমস্ত পদ।
সমস্যমান পদ:
সমস্যমান পদ: সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অর্ন্তগত পদগুলোকে বলা হয় সমস্যমান পদ।
যেমন: সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা। এখানে, ’সাহিত্য’, ’বিষয়ক’ এবং ’সভা’ পদগুলো-ই হলো সমস্যমান পদ।
সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ বা শব্দকে বলে পূর্বপদ এবং পরের অংশকে বলে পরপদ বা উত্তর পদ।
ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য:
সমস্ত পদকে ভাঙ্গলে যে বাক্যাংশ পাওয়া যায় তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বলে।
সমাসের প্রকারভেদ:
সমাস ছয় প্রকার:
১. দ্বন্দ্ব সমাস
০২. কর্মধারয় সমাস
০৩. তৎপুরুষ সমাস
০৪. দ্বিগু সমাস
০৫. বহুব্রীহি সমাস
০৬. অব্যয়ীভাব সমাস
সমাসের প্রকারভেদ:
সমাস ছয় প্রকার:
০১. দ্বন্দ্ব সমাস
০২. কর্মধারয় সমাস
০৩. তৎপুরুষ সমাস
০৪. দ্বিগু সমাস
০৫. বহুব্রীহি সমাস
০৬. অব্যয়ীভাব সমাস
দ্বন্দ্ব সমাস:
যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।
যেমন: মাতা ও পিতা = মাতাপিতা , দা ও কুমড়া = দা-কুমড়া, তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম ইত্যাদি।
দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও উত্তর পদের মাঝখানে এবং, ও, আর – এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়।
দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমন:
১. মিলনার্থক দ্বন্দ্ব: মাতা-পিতা, মাসি-পিসি, জি¦ন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
২. বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব: স্বর্গ-নরক, অহি-নকুল, দা-কুমড়া ইত্যাদি।
৩. বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব: আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, ছোট-বড় ইত্যাদি।
৪. সমার্থক দ্বন্দ্ব: হাট-বাজার, খাতা-পত্র, কল-কারখানা, ঘর-দুয়ার ইত্যাদি।
৫. প্রায় সমার্থক বা সহচড় দ্বন্দ্ব: কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া ইত্যাদি।
৬. অঙ্গবাচক শব্দযোগে: হাত-পা, নাক-মুখ, নাক-কান, মাথা-মুন্ডু ইত্যাদি।
৭. সংখ্যাবাচক দ্বন্দ্ব: সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।
৮. দুটি সর্বনাম যোগে: তুমি-আমি, যে-সে, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
৯. দুটি বিশেষণযোগে: ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল ইত্যাদি।
১০. দুটি ক্রিয়াযোগে: চলা-ফেরা, যাওয়া-আসা, দেখা-শোনা ইত্যাদি।
১১. দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে: ধিরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে ইত্যাদি।
অলুক দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না তাকে আলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে, দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে, জলে ও স্থলে = জলে-স্থলে ইত্যাদি।
বহুপদি দ্বন্দ্ব: দুইয়ের অধিক পদ নিয়ে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসকে বহুপদি দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম।
কর্মধারয় সমাস:
বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের মিলনে যে সমাস হয় এবং পর পদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।
যেমন: স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ, নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু।
মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস:
ব্যাসবাক্যের মধ্যপদ লোপ পেয়ে যে, সমাস হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন। সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা।
উপমান কর্মধারয় সমাস:
উপমান শব্দের অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনা করা হলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয় এবং যার সাথে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমান। ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে, ভ্রমর হলো উপমান এবং কেশ হলো উপমেয়। উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে একটি সাধারণ গুন বা ধর্ম বিদ্যমান থাকে। ভ্রমর ও কেশের মধ্যে সাধারণ গুন বা ধর্ম হলো ’কৃষ্ণত্ব’।
উপমিত কর্মধারয় সমাস:
কোন গুনের উল্লেখ না করে প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এক্ষেত্রে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যকার গুন বা ধর্মটি অনুমান হয়। উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে।
যেমন: পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ। মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ।
রূপক কর্মধারয় সমাস:
উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করে যে, সমাস হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে। ’রূপ’ বা ’ই’ প্রত্যয় যোগে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়। যেমন: মন রূপ মাঝি = মনমাঝি। বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু। ক্রোধ রূপ অনল = ক্রোধানল।
তৎপুরুষ সমাস:
পূর্বপদে বিভক্তির লোপ পেয়ে যে সমাস হয় এবং পর পদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।
পূর্বপদের বিভক্তি অনুযায়ি এ সমাসের নামকরণ করা হয়। যেমন:
১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস:
পূর্ব পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: দু:খকে প্রাপ্ত = দু:খপ্রাপ্ত। বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।
ব্যাপিয়া বা ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: চিরকাল ব্যাপিয়া সুখি = চিরসুখি।
২. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস:
পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কতৃক) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: শ্রম দ্বারা লদ্ধ = শ্রমলদ্ধ। মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা। মন দিয়ে গড়া = মনগড়া।
উত্তর পদ বা পরপদ হিসেবে ঊন, হীন বা শূন্য প্রভৃতি শব্দ থাকলে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন: এক দ্বারা ঊন = একোন। জ্ঞান দ্বারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য। বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন।
৩. চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস:
পূবপদে চতুর্থ বিভক্তি ( কে, জন্য, নিমিত্ত)- এর লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি। বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় = বালিকা বিদ্যালয়। বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি।
৪. পঞ্চমি তৎপুরুষ সমাস:
পূর্বপদে পঞ্চমি বিভক্তি ( হতে, থেকে, চেয়ে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে পঞ্চমি তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো। শাপ থেকে মুক্ত = শাপমুক্ত। বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত। খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া।
৫. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস:
পূর্ব পদে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) লোপ পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: দিল্লীর ইশ^র = দিল্লীশ^র। ছাত্রদের সমাজ = ছাত্রসমাজ। রাজার পুত্র = রাজপুত্র। বিড়ালের ছানা = বিড়ালছানা।
অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস:
পূর্ব পদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপ না পেয়ে যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: মামার বাড়ি = মামার বাড়ি। ঘোড়ার ডিম = ঘোড়ার ডিম। হাতের পাঁচ = হাতের পাঁচ। মনের মানুষ = মনের মানুষ। কলের গান = কলের গান।
৬. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস:
পূর্ব পদে সপ্তমী বিভক্তির ( এ, য়, তে ) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: গাছে পাকা = গাছপাকা। অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু। দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা। রাতে কানা = রাতকানা।
৭. নঞ্ তৎপুরুষ সমাস = পূর্ব পদে না বাচক বা নঞ্ অব্যয় ( না, নেই, নাই, নয় ) যোগে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: ন আচাড় = অনাচাড়। ন কাতর = অকাতর। নেই আদর = আনাদর।
৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাস =
৯. অলুক তৎপুরুষ সমাস:
দ্বিগু সমাস:
পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ পরে সমাহার থাকলে দ্বিগু সমাস হয়।
চার রাস্তার সমাহার = চৈৗরাস্তা
চার চালের সমাহার = চৌচালা
পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী
বহুব্রীহি সমাস:
বহুব্রীহি আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে, বহু অর্থ অনেক এবং ব্রীহি অর্থ ধান কিন্তু বহুব্রীহি অর্থ অনেক ধান নয় বরং বহু বা অনেক ধান আছে এমন অবস্থাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি। তাই বলা যায়, পূর্বপদ বা পরপদ কোন পদের অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে বরং অন্য তৃতীয় কোন অর্থ প্রাধান্য পেলে তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।
বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি। এখানে, বীণা (বাদ্যযন্ত্র) বা পাণি (হাত) না বুঝিয়ে বরং বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে বোঝায়।
দশ আনন যার = দশানন। এখানে, সংখ্যা দশ বা আনন (মাথা) অর্থ প্রাধান্য পায় না। বরং দশটি মাথা থাকায় লঙ্কার রাজা রাবনকে বোঝায়।
বহুব্রিহী সমাসের প্রকার ভেদ:
বহুব্রিহী সমাস আট প্রকার:
১। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি:
পূর্বপদে বিশেষণ ও পরপদে বিশেষ্য মিলে যে বহুব্রিহী সমাস হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রিহী সমাস বলে। যেমন: হৃত হয়েছে সর্বস্ব যার = হৃতসর্বস্ব। খোশ মেজাজ যার = খোসমেজাজ। নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ।
২। ব্যধিকরণ বহুব্রিহী সমাস:
৩। মধ্যপদলোপী বহুব্রিহী সমাস:
৪। প্রত্যয়ান্ত বহুব্রিহী সমাস:
৫। ব্যতিহার বহুব্রিহী সমাস:
৬। নঞর্থক বহুব্রিহী সমাস:
৭। সংখ্যাবাচক বহুব্রিহী সমাস:
৮। অলুক বহুব্রিহী সমাস:
অব্যয়ীভাব সমাস:
অব্যয়ীভাব শব্দটির অর্থ অব্যয়ের ভাব বর্তমান। পূর্ব পদে অব্যয় পদের সমন্বয়ে যেখানে পূর্বপদ বা অব্যয়েরই অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদে অব্যয় বা উপসর্গ এবং পরপদে বিশেষ্য থাকে এবং অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়।
বিভিন্ন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ:
১। সামীপ্য (উপ) : কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে = উপকূল ইত্যাদি।
২। পর্যন্ত (আ) : পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক, সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল।
৩। বিরোধ অর্থে (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল ইত্যাদি।
৪। বিপ্সা অর্থে (অনু, প্রতি) : ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে, দিন দিন = প্রতিদিন ইত্যাদি।
৫। সাদৃশ্য অর্থে (উপ) : শহরের সদৃশ্য = উপশহর, বনের সদৃশ = উপবন, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ।
৬। পশ্চাৎ অর্থে (অনু) : পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, পশ্চাৎ ধাবন = অনুধাবন ইত্যাদি।
৭। অভাব অর্থে (নি: = নির) : জলের অভাব = নির্জল, আমিষের অভাব = নিরামিষ, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।
৮। ঈষৎ অর্থে (আ) : ঈষৎ নত = আনত, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম।
৯। দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর) = অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ।
১০। প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি) : প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর।